বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন
হোমেন বরগোহাঞি
মূল অসমিয়া থেকে বাংলা অনুবাদ– বাসুদেব দাস (Basudeb Das)
নয়
(৯)
বেচারা রিচার্ডের বর্ষপুঞ্জী
(Poor Richards Almanac)
(Poor richards Almanac) বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলিন ইতিমধ্যে ফিলাডেলফিয়ার একজন নেতৃস্থানীয় ধনী মানুষ বলে পরিচিতি লাভ করেছেন।
১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেঙ্কলিন তার ছাপা ছাড়া থেকে প্রতিবছর একটি বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি বর্ষপঞ্জিটার নাম দেন–Poor richards Almanac–অর্থাৎ বেচারা রিচার্ডের বর্ষপঞ্জী। রিচার্জ ছিলেন একটি কাল্পনিক চরিত্র। মানুষটা ছিলেন অতি সৎ, কিন্তু অতি দরিদ্র।স্ত্রীর কাছ থেকে গালিগালাজ খেয়েই তাঁর দিন কাটে। প্রকাশ ফ্রাঙ্কলিন প্রতিবছর প্রকাশ করা বর্ষপঞ্জিটা ছিল রিচার্ড নামে এই কাল্পনিক মানুষটির স্বীকারোক্তি।। নিজের জীবনের কথা বলার ছলে রিচার্ড নানা বিষয়ে তার মন্তব্য এবং নীতি উপদেশ দিতেন। সেই প্রতিটি কথা তিনি লিখেছিলেন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বেচারার রিচার্ডের বর্ষপঞ্জি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, ফ্রেঙ্কলিনকে প্রতিবছর বর্ষপঞ্জীটার দশ হাজার কপি প্রকাশ করতে হয়েছিল। সুদীর্ঘ 25 বছর কাল বর্ষপঞ্জীটি প্রকাশ হয়েছিল। এই বর্ষপঞ্জটি একইসঙ্গে তিনটা কাজ করেছে। প্রথমত, এটি আমেরিকার মানুষের স্বভাব চরিত্র উন্নত করা এবং জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করায় সাহায্য করেছে। দ্বিতীয়ত,বর্ষপঞ্জীটি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের চেয়ারটি এবং জনপ্রিয়তা আমেরিকার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, বর্ষপঞ্জী থেকে ফ্রেঙ্কলিন এত ধন উপার্জন করলেন যে তিনি সেই সময়ের আমেরিকার প্রথম সারির ধনীদের মধ্যে একজন বলে পরিচিতি লাভ করলেন।
বেচারা রিচার্ডের বর্ষপঞ্জীর কিছু যোজনা পাঠান্তরের পরিচিতি নিচে দেওয়া হল–
নিজের নিকটতম প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে, কিন্তু দুটি বাড়ির মধ্যে সীমানাটা ভেঙ্গে ফেল না।
তোমার নিজের ভাই তোমার বন্ধু না হতে পারে, কিন্তু তোমার বন্ধু সবসময় তোমার ভাই হয়ে থাকবে।
মানুষ মাত্রই ভুল করে; ক্ষমা করাটা স্বর্গীয় গুণ; কিন্তু একই ভুলকে বারবার করে থাকাটা শয়তানের লক্ষণ।
‘ কর্কশ’ শব্দ প্রয়োগ করে কেউ কারও বন্ধু হতে পারে না। এক গ্যালন ভিনেগারের চেয়ে এক চামচ মধু দিলে বেশি মাছি ধরা পড়বে।
যে মানুষ সুখ শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়, তিনি নিজে সমস্ত কথা মুখ খুলে বলেন জানা সমস্ত কথা মুখ খুলে বলেন না, আর নিজে দেখা সমস্ত কথার উপরে মন্তব্য করেন না।
একজন সহজ সরল গ্রামের মানুষ যদি উকিলের পাল্লায় পড়ে; তাহলে তার অবস্থা হয় দুটি বিড়ালের মধ্যে পড়া মাছের মতো।
পচা আপেল একটি টুকরিতে থাকলে বাকি আপেলগুলি পচতে আরম্ভ করে।
কোনো মানুষ এত খারাপ হতে পারেন না যে তিনি অন্যের ভালো গুণগুলিকে শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারেন।
সহজ উদাহরণই হল সর্বোত্তম উপদেশ।
নিজের বিবেক সব সময় নির্মল করে রাখবে; তাহলে তুমি অন্যকে ভয় করে চলার প্রয়োজন নেই।
যে মানুষ আদেশ পালন করতে পারে না, তিনি অন্যকে আদেশ দিতে পারেন না।
মিথ্যা কথা আর একটি, সত্যের পা দুটি।
সমস্ত মানুষকে খুব সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণ করবে নিজেকে।
জীবন দীর্ঘ হলেও সে ভালো জীবন নাও হতে পারে; কিন্তু ভালো জীবন সব সময় দীর্ঘ বলে প্রমাণিত হয়।
জীবন ধারণের জন্য খাবে,? খাবার জন্য জীবন ধারণ করবে না।
যে মানুষ কারও কাছ থেকে কিছু আশা করে না , তিনিই সুখী এবং ভাগ্যবান মানুষ। তাকে জীবনে কখনও বিরাশ হতে হয় না।
তুমি সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাও কি? যদি চাও, তাহলে যে কাজ করা উচিত, কেবল সেই কাজই করবে, যে কাজ করে খুশি হও, সেরকম কাজ করবে না।
যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চাও, তাহলে আহারের পরিমাণ পরিমাণ কম করবে।
পিঁপড়ার চেয়ে ভালো নীতি শিক্ষা অন্য কেউ দিতে পারে না; পিঁপড়া কিন্তু মুখে কিছু বলে না।
কষ্ট না করে কেউ কিছু জিনিস লাভ করতে পারে না।
দোকানটা ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে;তখন দোকানটাও তোমাকে সুখে-সন্তোষে রাখবে।
যে মানুষ পরিশ্রম করে না,সে কখনও খ্যাতিমান হতে পারে না।
আগামীকাল কিছু কাজ করার মতো আছে কি?যদি থাকে তাহলে সেই কাজ আজই করে ফেল।
একজন যুবক ব্যবসায়ীর প্রতি উপদেশ
তোমার চাহিদা অনুসারে আমি নিচে কয়েকটি সংকেত দিলাম।আমি নিজে এই কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে জীবনে অনেক সুফল পেয়েছি।আমি আশা করি যে তুমিও আমার মতোই সুফল পাবে।
মনে রাখবে যে সময়ই হল ধন।ধরে নাও,তুমি সারাদিন কাজ করে দশ শিলিং রোজগার করতে পার।কিন্তু তুমি মাত্র অর্ধেক দিন কাজ করে দিনটির বাকি সময় শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলে।সেই সময়ে তুমি যেন আমোদ-প্রমোদের জন্য ছয় শিলিং খরচ করলে।তুমি ভাবলে যে তুমি মাত্র ছয় শিলিংই খরচ করেছ।কিন্তু আসলে খরচের তালিকায় তোমাকে আরও পাঁচ শিলিং যোগ দিতে হবে।কারণ দিনের অর্ধেক ভাগ সময় তুমি শুয়ে বসে বা রং তামাসা করে না কাটালে তুমি পাঁচ শিলিং অর্জন করতে পারতে।
মনে রাখবে যে ধনের নিজের সংখ্যা-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে।ধন সন্তানের জন্ম দান করে;ধনের সন্তান নতুন করে সন্তানের জন্ম দান করে।এভাবে ধনের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে।পাঁচ শিলিং ভালোভাবে ব্যাবসায় বিনিয়োগ করতে জানলে তা একদিন ছয় শিলিং হবে।ছয় শিলিং অতি দ্রুত সাত শিলিং তিন পেন্স হবে।এভাবে বাড়তে বাড়তে তা একদিন গিয়ে একশো পাউণ্ড হবে।ব্যাবসায় ভালো হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে লাভও দ্রুত গতিতে বাড়তে শুরু করবে।কেউ যদি বাচ্চা দিতে থাকা অবস্থায় একটি শূকরীকে মেরে ফেলে ,তাহলে সে ভবিষ্যতে হাজারটা পুরুষের জন্য শূকরীটির সবগুলি বংশধরকে হত্যা করে।ঠিক সেভাবে কেউ যদি একটি শিলিং নষ্ট করে তিনি আসলে সেই শিলিংটা থেকে হতে পারা শত শত পাউণ্ড নষ্ট করেন।
মনে রাখবে যে, যে মানুষ অন্যের কাছ থেকে ধন ধারে নিয়ে সেই ধার সময়মতো পরিশোধ করেন তিনি আসলে অন্যের ধনের থলেগুলির মালিক হন।যখন মানুষ দেখে একজন মানুষ অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া সমস্ত টাকা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করে,অর্থাৎ তিনি নিজের শপথ রক্ষা করেন,তখন তাঁর প্রয়োজন হলেই অন্যে তাকে ধন ধার দিতে সঙ্কোচ করে না।ব্যাবসায়ী মানুষকে এই কথাটা খুব সাহায্য করে।ব্যাবসায় উন্নতি করতে চাওয়া যে কোনো যুবকের জন্য অধ্যবসায় এবং মিতব্যয়িতার পরেই সবচেয়ে বড়োগুণ হল আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা।সেইজন্য কারও কাছ থেকে ধন ধারে নিলে ধার পরিশোধ করা নির্দিষ্ট সম্যের চে্য়ে মাত্র একঘণ্টা সময়ও বেশি সেই ধন নিজের হাতে রাখবে না,কারণ তাহলে তুমি পুনরায় কখনও বন্ধুদের কাছ থেকে ধন ধারে পাওয়ার আশা করতে পারবে না।
তুমি যার কাছ থেকে ধন ধারে নাও তাঁর মনে তোমার সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মাতে পারা ছোটো ছোটো কথাগুলি সযত্নে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করবে।তোমার কারখানায় যদি সকালবেলা পাঁচটার সময় বা রাত নয়টার সময় হাতুড়ির কাজ চলতে থাকে এবং তোমাকে টাকা ধার দেওয়া মানুষটি সেই হাতুড়ির শব্দ শুনতে পায়,তাহলে তিনি তোমার হাতে তার ধনটুকু আরও ছয়মাস বেশিদিনের জন্য ছেড়ে দিতে দ্বিধা করবে না।কিন্তু অন্যদিকে তুমি যে সময়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকা উচিত ছিল সেই সময়ে যদি তিনি তোমাকে তাস খেলায় মত্ত থাকতে বা মদের দোকানে দেখতে পায়,তাহলে ঠিক তার পরদিনই তিনি তোমার কাছ থেকে ধনটুকু ফিরে পাবার দাবি জানাবে।
সবসময় আয় দেখে ব্যয় করবে।তা না করলে নিজের অজান্তেই তুমি একদিন ঋণী হয়ে পড়বে এবং ধারের বোঝা ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকবে।
সেরকম যাতে না হয় তার জন্য তুমি কিছুদিনের জন্য তোমার উপার্জন এবং খরচের হিসেব লিখে রাখার হিসেব করবে।তুমি যদি একটু কষ্ট করে খরচের খুঁটিনাটিগুলি লিখে রাখ,তাহলে খুচরো খরচগুলি কীভাবে একদিন গিয়ে একটা মোটা অঙ্কে পরিণত হয় সেকথা তুমি নিজেই আবিষ্কার করবে।তখন তুমি নিজের জন্য বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি না করে ধন সঞ্চয় করতে শিখবে।
সংক্ষেপে বলতে গেলে ধনী হওয়ার পথটা বাজারে যাওয়া পথের মতোই সোজা।এটা প্রধানত নির্ভর করে মাত্র দুটি শব্দের ওপরে।অধ্যবসায় এবং মিতব্যয়িতা।অর্থাৎ সময় এবং ধন এই দুটির একটিরও অপচয় করবে না;বরং দুটিরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে।অধ্যবসায় এবং মিতব্যয়িতার অবিহনে তুমি কখনও ব্যাবসায়ে সফল হতে পারবে না।অন্যদিকে এই দুটি একত্রিত হলে তুমি ব্যাবসায় সফল না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।যে মানুষ সৎভাবে পেতে পারা সমস্ত ধন পায় এবং পাওয়া ধনটুকু (অত্যাবশ্যকীয় খরচটা বাদ দিয়ে)সঞ্চয় করে তিনি নিশ্চয় একদিন ধনী মানুষ হবেই হবে।
যে মানুষ ভাবে যে নিজের জোরে তিনি সমস্ত কাজ করিয়ে নিতে পারেন,তাহলে সেরকম মানুষকে এই বলে সন্দেহ করার জন্য জায়গা থাকে যে তিনি প্রত্যেকটা কাজ ধনের জন্য করেন।
কুঠারের একটু একটু আঘাতে একটি বিরাট গাছ গড়িয়ে ফেলতে পারে।
তুমি যত অর্জন কর,তারচেয়ে কম খরচ করার জন্য যদি শেখ,তাহলে নিশ্চয় জানবে যে সমস্ত জিনিসকে সোনায় পরিণত করতে পারা প্রশ-পাথর তুমি পেয়ে গেছ।
তাড়াতাড়ি বিছানায় যাওয়া এবং দ্রুত উঠার অভ্যাস করবে;তখন তুমি স্বাস্থ্যবান,ধনী এবং জ্ঞানী হতে পারবে।
গাড়ির সবচেয়ে খারাপ চাকাটা সবচেয়ে বেশি শব্দ করে।
কৃ্তকার্যতা অনেক মানুষের সর্বনাশ করেছে।
নিজের জ্ঞান গোপন করতে না পারা মানুষের চেয়ে বড়ো মূর্খ অন্য কেউ নেই।
ছোটো ছোটো দষ-ত্রুটিগুলি সময় মতো শুধরে না নিলে শেষে এটাই গিয়ে বিরাট আকার ধারণ করে।
কাঁচের বাসন,চিনা মাটির বাসন এবং মানুষের খ্যাতি অতি সহজে ভাঙে;সেইসব কখনও সম্পূর্ণভাবে জোড়া লাগে না।
যে নিজেকে সহায় করে,তাকে ঈশ্বরও সহায় করে।
ক্ষুধাই হল সবচেয়ে ভালো তরকারি।
অভিজ্ঞতার পাঠশালা অতিমাত্রায় খরচে
কিন্তু মূর্খ তার বাইরে অন্য কিছু পাঠশালায় শিখতে পারে না।
যে মানুষের কাঁটা ছড়ানো অভ্যাস,তার কখনও খালি পায়ে হাঁটা উচিত নয়।
তিনজন মানুষের পক্ষে একটা গোপনীয় কথা গোপন করে রাখা সম্ভব-যদি সেই তিনজন মানুষের ভেতরে দুজন মানুষের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়।
কুয়ো শুকিয়ে তলা বেরিয়ে গেলে তবেই আমরা জলের মূল্য বুঝি।
সময় হল এমন একটি মহৌষধের ,যা সমস্ত ধরনের রোগ নিরাময় করতে পারে।
কেবল জ্ঞানী এবং সাহসী মানুষ নিজের ভুলটা স্বীকার করতে পারে।
খারাপ ইস্পাত দিয়ে কখনও ভালো দা তৈরই করা যায় না।
তুমি যদি তোমার শত্রুর কোনো অপকার কর,তাহলে তুমি তোমার শত্রুর চেয়ে নিচু স্তরের মানুষ বলে পরিগণিত হবে।
তুমি যদি শত্রু তোমার করা অপকারের প্রতিশোধ নিতে চাও,তাহলে তুমি তোমার শত্রুর একই সারির মানুষ বলে গণ্য হবে।কিন্তু যদি শত্রু তোমার প্রতি করা অপকারের জন্য তুমি তাকে ক্ষমা করে দিতে পার,তাহলে প্রমাণ করা হবে যে তুমি তোমার শত্রুর চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ।
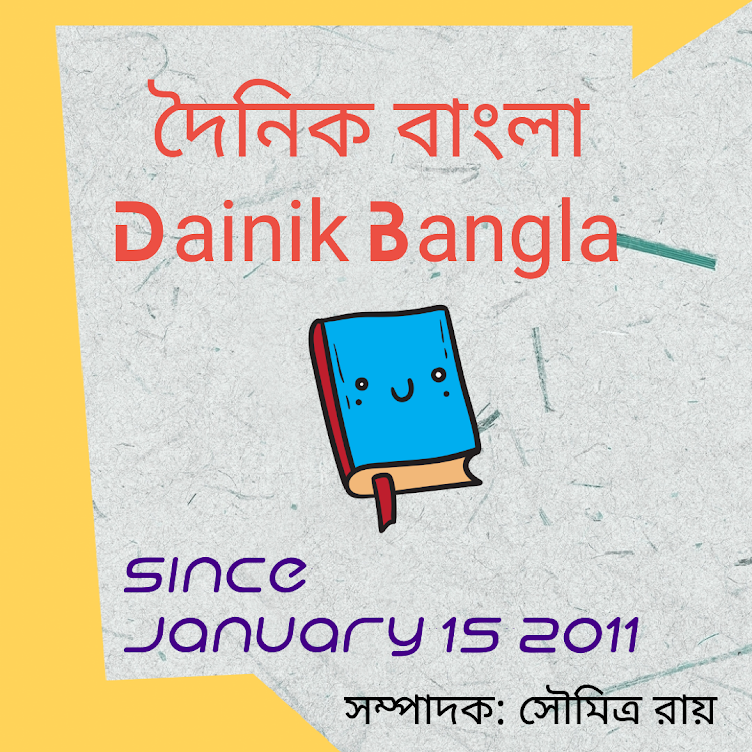
.jpeg)



